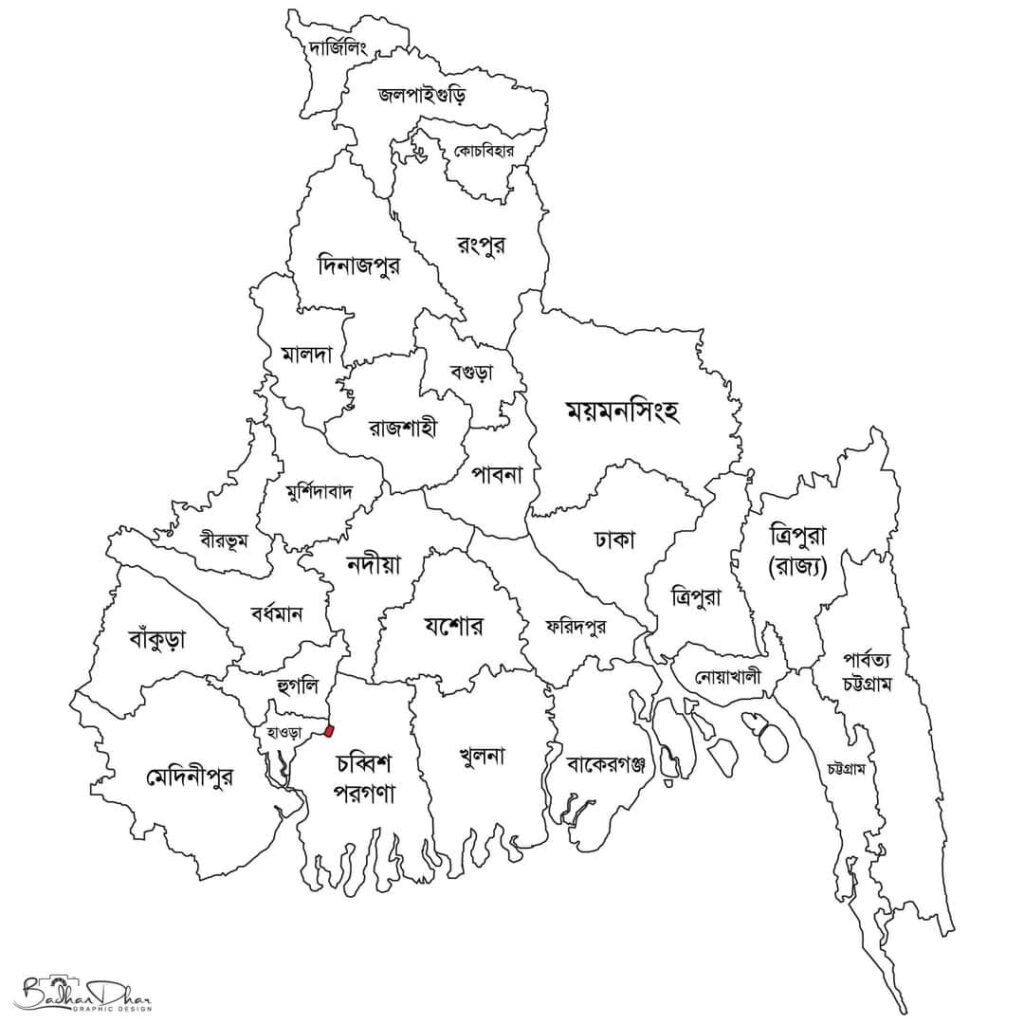বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষঃ একটি বিশ্লেষণ
বিমল প্রামাণিক ‘পাকিস্তানি বাধা অতিক্রম করে মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ যখন উন্মুক্ত হল তখন তার সামনে সমস্যা দেখা দিল আরেকটি। ভারত বড় প্রতিবেশী। শুধু আয়তনে নয়, অর্থনীতিসহ সব দিক দিয়েই বাংলাদেশের তুলনায় ভারত অগ্রসর। আর ভয় সেখানেই। এভয় হল ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর বৃহৎ সম্পর্ক-ভীতি। তার উপর দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে অবিশ্বাস বা বিদ্বেষের যে পটভূমিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছিল মাঝের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তা দূরীভূত হয়েছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। ফলে স্বাধীনতার পরে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত সম্পর্কে সন্দেহের ভাব যখন দেখা দিল মধ্যবিত্তের মনে, তখন স্বাভাবিকভাবে সম্প্রদায়গত বিভেদের ইতিহাসও সামনে এসে দাঁড়াল। আর এদের সাথে একাংশের ভিতর পাকিস্তানের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারও অস্বাভাবিক মনে হল না। আর ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শীতলতা যত বেড়েছে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। বস্তুত বাঙালি মধ্যবিত্তের মাঝে একদিকে মুক্তিযুদ্ধ বা তার আগের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে ভারত সম্পর্কে সন্দেহ-অবিশ্বাস (যা অতীত সম্প্রদায়গত বিভেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিপোষিত) – এই দু’য়ের টানাপোড়েন বিদ্যমান। আর এই টানাপোড়েনেই বাঙালি না মুসলমান, না মুসলমান বাঙালি, না বাঙালি মুসলমান এই দোলাচলে অভিব্যক্ত।’ ১ আজকের বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে ভারত বিদ্বেষের যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কোন নতুন বিষয় নয়। এর শিকড় দ্বিজাতিতত্ত্বের গভীরে নিহিত ছিল। এর প্রকট প্রকাশ ধরা পরে হিন্দু বিদ্বেষের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায়। পাকিস্তানের ‘যোগাযোগ মন্ত্রী’ শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৫০ সালেই তার সুদীর্ঘ ইস্তফাপত্রে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের হিন্দু-বিতাড়নের নীতি ও কার্যকলাপের যে বিস্তারিত বিবরণ লিখে গেছেন তা থেকে কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ “Pakistan `Accursed’ for Hindus Now this being in brief the overall picture of Pakistan so far as the Hindus are concerned, I shall not be unjustified in stating that Hindus of Pakistan have to all intents and purposes been rendered “stateless” in their own houses. They have no other fault than that they profess Hindu religion. Declarations are being repeatedly made by Muslim League leaders that Pakistan is and shall be an Islamic State. Islam is being offered as the sovereign remedy for all earthly evils. In the ruthless dialectics of capitalism and socialism you present the exhilarating democratic synthesis of Islamic equality and fraternity. In that grand setting of the Shariat Muslims alone are rulers while Hindus and other minorities are jimmies who are entitled to protection at a price, and you know more than anybody else, Mr. Prime Minister, what that price is. After anxious and prolonged thought I have come to the conclusion that Pakistan is no place for Hindus to live in and that their future is darkened by the ominous shadow of conversion or liquidation. The bulk of the upper class Hindus and politically conscious scheduled castes have left East Bengal. These Hindus who will continue to stay in the accursed province and for that matter in Pakistan will, I am afraid, by gradual stages and in a planned manner be either converted to Islam or completely exterminated. It is really amazing that a man of your education, culture and experience should be an exponent of a doctrine fraught with so great a danger to humanity and subversive of all principles of equity and good sense. I may tell you and your fellow workers that Hindus will never allow themselves, whatever the thereat or temptation, to be treated as jimmies in the land of their birth. Today they may, as indeed many of them have already done, abandon their hearths and homes in sorrow but in panic. Tomorrow they will strive for their rightful place in the economy of life. Who knows what the womb of the future is? When I am convinced that my continuance in office in the Pakistan Central Government is not of any help to Hindus I should not, with a clear conscience, create the false impression in the minds of the Hindus of Pakistan and peoples abroad that Hindus can live there with honour and with a sense of security in respect of their life, property and religion. This is about Hindus.”2 পাকিস্তান সরকারের যে ভারত তথা হিন্দু বিদ্বেষী নীতি ও কার্যকলাপ এবং তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র চব্বিশ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১) মধ্যেই তিনবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লাগাতার হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা ও কালা কানুন ( Enemy Property ordinances and laws উল্লেখযোগ্য) জারী করে হিন্দু নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় পাকিস্তানের মুসলমান সম্প্রদায় ভারতকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এর প্রধান সুবিধাভোগী ছিল উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও ক্ষমতাশালী মুসলমান সম্প্রদায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন বা করছেন তারা ভারত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবেন কী করে ! ভারত বিদ্বেষের মধ্যেই যাদের জন্ম এবং বংশ পরম্পরায় বেড়ে ওঠা সেই পাকিস্তানি সংস্কৃতির আবহে, তা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনের উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রারম্ভেই তার একটা চেষ্টার অঙ্কুর দেখা গেলেও অচিরেই তা রুদ্ধ হয়ে যায়। আর ১৯৭৫-এর কালান্তক ঘটনার পর বাংলাদেশের শরীরে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা জাঁকিয়ে বসতে কাল বিলম্ব করেনি। বিশিষ্ট গবেষক নুহু-উল-আলম লেনিন ‘সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ’ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে থাবা বিস্তার করেছে, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় সৃষ্ট পাকিস্তানের সমকালীন কবি- সাহিত্যিকরা অনেকেই তাই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক সবকিছুতেই এর ছাপ পড়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র কাঠামোতে নানা পরিবর্তন সাধিত হলেও সাম্প্রদায়িক চেতনার সাহিত্যিকেরা ধর্মীয় ও পশ্চাদপদ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আসতে পারানি। … কিন্তু ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।” … আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি “আল মাহমুদ পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সবকিছু মূল্যায়ণ করেছেন। বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি যেমন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা সমর্থন করেছেন, তেমনি সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি। বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সব কিছুতে ইসলাম আর মুসলমান লেবেল এঁটে দিয়েছেনঃ বাংলাদেশ মূলত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এখানে সাড়ে এগারো কোটি নর-নারীর মধ্যে দেড় কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান বাদে আর সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী । ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ইসলামের বিধিনিষেধ সমূহ এখানকার জনজীবনে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপালিত হচ্ছে। এমনকি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। এখানকার আদব-কায়দা, প্রাত্যহিক সামাজিক বিনিময়ে, পোশাক-আশাকে, খাদ্য রুচিতে এবং সর্বোপরি সাধারণ সামাজিক সম্মিলনের ক্ষেত্রগুলোতেও অচেতনভাবে হলেও ইসলামের হালাল-হারাম পাত্তা পেয়ে আসছে। পারস্পরিক সাক্ষাৎ মুহুর্তে আমরা …